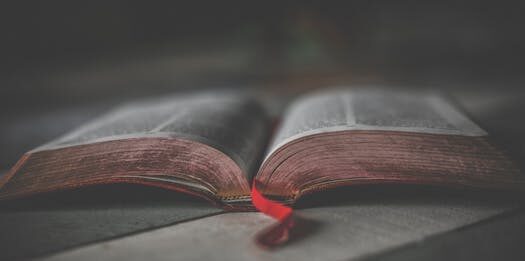কারবালার প্রচলিত কাহিনী সংক্ষেপে এরকম : উসমান (রাঃ) এর মৃত্যুর পরে মুসলিম জাহানের খিলাফত নিয়ে বিতন্ডা শুরু হয়। অধিকাংশ মুসলমান হযরত আলী (রাঃ) কে খলিফা মেনে নিলেও একটা গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করেন। খারেজি নামে একটি গোষ্ঠীরও উদ্ভব ঘটে তখন। ৫ বছরের শাসন শেষে আততায়ীর হাতে নিহত হন হযরত আলী (রাঃ)। এরপর মুয়াবিয়া ইরাক থেকে নিজেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা হিসেবে ঘোষণা করলে দেখা দেয় বিপত্তি। অনেকেই তখন এই পদের জন্য আলীতনয় হাসান (রাঃ) কে যোগ্য বলে মত দেন। দেখা দেয় বিভেদ। মুয়াবিয়া (রাঃ) পরে হাসান (রাঃ) এর সাথে এক চুক্তি করেন যে তার মৃত্যুর পরে মজলিসে সুরার পরামর্শক্রমেই নির্বাচিত হবেন পরবর্তী খলিফা। কিন্তু এই চুক্তি অমান্য করে মুয়াবিয়াপুত্র এজিদ নিজেকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে গোপনে বিষ দিয়ে হযরত হাসান (রাঃ) কে মেরে ফেলা হয়। এজিদ খলিফা হলে তার বিরোধিতা করেন ইমাম হোসেন (রাঃ) ও তার অনুসারীরা। তাকে সমর্থন দেন ইরাকের অন্যতম প্রদেশ কুফার জনগন। তাদের সমর্থন নিয়ে এজিদের মোকাবেলা করার জন্য অনুসারীদের নিয়ে হযরত হোসেন(রাঃ) রওনা দেন কুফার দিকে। পথিমধ্যে কারবালা নামক স্থানে তিনি এজিদের বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত ও শহীদ হন। এজিদের খিলাফত অব্যাহত থাকে।
প্রচলিত ইতিহাস, লোকগাঁথা বা শিল্পসাহিত্যে যেভাবে চিত্রায়িত হয়েছে কারবালার কাহিনী তা কতটা বাস্তবিক, কতটা অতিরঞ্জিত তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। মাবিয়া পুত্র এজিদ নাকি সুমাইয়ার পুত্র ইবনে জিয়াদ এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিতর্ক আছে। অনেকে বলেন ইমাম হোসেনের মৃত্যুতে এজিদ সারাজীবন অশ্রুপাত করে বেরিয়েছেন। এই ব্যাপারে সাক্ষীদাতার সংখ্যাও অনেক। যেমন, ইমাম ইবনে তাইমীয়া (র.) বলেছেন, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া হুসাইন (রাঃ) কে হত্যার আদেশ দেন নি। বরং তিনি উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে চিঠির মাধ্যমে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন ইরাকের জমিনে হুসাইন (রাঃ) কে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দেন। এতটুকুই ছিল তার ভূমিকা। ইমাম হোসেনের হত্যাকন্ডে ক্ষুদ্ধ হয়ে এজিদ সীমারকেও মৃতুদণ্ড দিয়েছিলেন এরকম মতও আছে।
২. কারবালার কাহিনীর উৎস আবু মিখনাফ
নবীজীর (সাঃ) ইন্তেকালের পরে ঘটে যাওয়া কারবালার যুদ্ধের মতো ঘটনাগুলির বেশিরভাগই ইবনে ইসহাক নয় বরং আল-তাবারির (মৃত্যু ৯২৩ খ্রীস্টাব্দ) মতো পরবর্তী ঐতিহাসিকদের সূত্রে জানা যায়। নবীর মৃত্যু থেকে প্রায় ৩০০ বছর এবং কারবালার ঘটনা থেকে প্রায় ২৫০ বছর পরে আল-তাবারি তাঁর কাছে পৌঁছেছে এমন বিবরণ গুলি ব্যবহার করেছেন কারবালার কাহিনী বর্ণনায়।
‘তারিখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলুক’ (নবী ও রাজাদের ইতিহাস) শিরোনামে আল-তাবারির বিশাল রচনাটি ১০ শতক অব্দি সময়কালকে বর্ণনা করে ইতিহাসের একটি উৎস হিসেবে রয়ে গেছে। তবে আল-তাবারির বইটির ভুমিকাটি প্রণিধানযোগ্য। সেখানে তিনি খুব পরিস্কার করেই বলেছেন যে, “যে আমার এই বইটি পড়বে বা পর্যালোচনা করবে তার জানা উচিত যে, আমি এখানে যা কিছু বর্ণনা করেছি সেসবের ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নির্ভর করেছি আমার কাছে যেসব বর্ণনা এসেছে সেসবের উপর। সেসবের মধ্যে যেগুলি যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় না সেগুলি বাদ দিয়েছি।”
এরপর, তাবারি নিজেই বলেছেন যে, এই বইয়ের কোন বিবরণ যদি পাঠকের কাছে আপত্তিজনক বা নিন্দনীয় বলে মনে হয় তাহলে তাকে বুঝতে হবে এর জন্য তিনি দায়ী নন। কারণ যারা তার কাছে এসব বিবরণ পৌছে দিয়েছেন তিনি কেবলমাত্র সেগুলি পরিবেশন করেছেন মাত্র।
তবে আল-তাবারিও কারবালার ঘটনার প্রাথমিক উৎস নন। প্রাচীনতম উৎস হলেন আবু মিখনাফ নামে একজন আরব যিনি ৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। একে ইবনে ইসহাকের সমসাময়িক বলা যায়। আল-তাবারি এই আবু মিখনাফের রচনাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন।
আবু মিখনাফের ‘কিতাব মাকতাল আল-হুসাইন’ এর মাধ্যমে আমরা কারবালার ঘটনার অনেক বিস্তারিত জানতে পারি। এখানে বলে রাখা ভালো, আবু মিখনাফের স্পষ্টতই শিয়া স্বার্থ ছিল এবং তার পিতামহ সিফফিনের যুদ্ধে জীবন দিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়, যে যুুদ্ধটি ৬৫৭ সালে আলী ইবনে আবি তালিব এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে হয়।
উল্লেখ্য, আবু মিখনাফের কোন মূল কাজের অস্তিত্ত্ব নেই। তার কাজ শুধুমাত্র তার ছাত্রদের মাধ্যমে এবং পরবর্তী ইতিহাসবিদ যেমন আল-তাবারির মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে।
আবু মিখনাফের কাজ সম্পর্কে কিছু গুরুতর সমালোচনাও রয়েছে। যেমন, আবু মিখনাফ সনদের পরম্পরা সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন না। তার বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে সিফফিন যুদ্ধের বর্ণনা, উপজাতীয় গল্প এবং স্থানীয় গসিপগুলি সন্নিবেশিত করার কারণে মুহাদ্দিস আলেমগণ তাকে দুর্বল উত্স হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনি তার নিজের গোত্রের গল্পের উপর অনেক বেশি নির্ভর করেছেন।
কখনও কখনও, তিনি মূল বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেন না এবং কেবল ‘সেখানে উপস্থিত ছিলেন এমন একজনের কাছ থেকে’, বা ‘বনু ফাজারা গোত্রের একজন সদস্যের কাছ থেকে’ পাওয়া গেছে এভাবে সূত্র উদ্ধৃত করেন।
এখন পর্যন্ত মাক্বতালের ৪টি পাণ্ডুলিপির সন্ধান মেলে। বার্লিন এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের দুটি পাণ্ডুলিপি থেকে একটা জর্মন অনুবাদ তৈরি করেছেন ফার্ডিনান্দ বুস্টেন্ডফেল্ড। এগুলি যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি তা নিয়ে তার মনে দ্বিধা নেই, কিন্তু এগুলি আবু মিখনাফের কি না তা তিনি নিশ্চিত নন বলে জানিয়েছেন।
তার আরেকটি পর্যবেক্ষণ হলো, এতে কিছু অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত ধরনের গল্প রয়েছে, যেমন প্রাকৃতিক ঘটনাতে দুঃখের ভয়ানক প্রকাশ: লাল হয়ে যাওয়া আকাশ, বালি থেকে রক্তক্ষরণ এবং এরকম আরও অনেক কিছু। এসব অলৌকিক কাহিনীর কিছু তাবারীতেও স্থান পেয়েছে।
তবে অলৌকতার বর্ণনার কারণে লেখক হিসেবে মিখনাফকে বাতিল করে দেওয়া সঙ্গত নয় বলে মনে করেন গবেষকরা। তাদের বক্তব্য,একজন মহান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা একটি বই অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাকে গ্রহণ করবে না এটা আশা করা ঠিক নয়, বিশেষ করে যখন মূল ঘটনাটিই যখন চরম দুঃখ কষ্ট ও আবেগমথিত।
কাজেকাজেই, শুদ্ধ ঐতিহাসিকতার বিচারে কারবালার বিস্তারিত বিবরণ আমরা যা পাই তার সকল বর্ণনা নিঃসংশয়ে কবুল করা মুশকিল। বিশেষ করে এই কাহিনীর আদিতম বর্ণনাকারীরাই যখন এর সত্যাসত্যের দায় নিতে নারাজ।
৩. শিল্প-সাহিত্যে কারবালা
শিল্পসাহিত্য বাস্তবের হুবহু অনুসরণ করবে এটা আশা করাও অবশ্য ঠিক নয়। ‘বিষাদ সিন্ধ’ুকে মীর মোশাররফ হোসেন নিজেও ইতিহাসগ্রন্থ বলে বর্ণনা করেননি।
সুন্নীপ্রধান বাংলাদেশে কারবালাকেন্দ্রিক শিল্পসাহিত্যের নমুনা খুব বেশি নেই। ‘বিষাদ সিন্ধু’ ছাড়া কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত ‘মোহররম’ সহ কিছু কবিতা ও শোকগীতি একমাত্র অবলম্বন।
তবে কারবালার কাহিনী যে শিয়া সাহিত্যকে কতটা অনুপ্রেরণা যোগায় সেটা টের পাওয়া যায় ইরান, ইরাক, লেবাননের দিকে তাকালে। বিশেষ করে ইরানে কারবালার কাহিনীর প্রেরণায় রচিত অসংখ্য নাটক প্রায়শই প্রদর্শিত হয়।
কয়েক বছর আগে লেবাননের কিছু এনিমেশন চলচ্চিত্রকার কারবালার কাহিনী নিয়ে তৈরি করেছেন এক সাহসী চলচ্চিত্র। সাহসী, কারণ সেবারই প্রথম চলচ্চিত্রে বিশ্বনবী (সাঃ) এর দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেন (রাঃ) কে একটি চরিত্র হিসেবে নিয়ে এসেছেন তারা। ‘আরজ আল তাফ’ নামের ওই ছবি মুক্তি পায় আশুরার সময়। ত্রিমাত্রিক এনিমেশনের ওই ছবিটি সুন্নীসহ অনেক মুসলিমদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছবির নেপথ্যে আছেন বৈরুত প্রোডাকশন এর পরিচালক আহমেদ হোমানি।
ইসলামে বিশিষ্টজনদের প্রতিকৃতি নির্মাণ নিষিদ্ধ বিধায় ‘আরজ আল তাফ’ ছবির নির্মাতারা এ ছবিতে ইমাম হোসেন (রাঃ) এর চেহারা একটা আলোকবলয় দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। চলচ্চিত্রে ইমামের চরিত্রে কণ্ঠস্বর দিয়েছেন লেবাননের দ্রুজ অভিনেতা জিহাদ আল আতরাশ।
এইসব গল্প, কবিতা, চলচ্চিত্রই মহররমের অফুরান প্রাণশক্তির অন্যতম উত্স হয়ে আছে এবং থাকবে। ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালাকে বাদ- এই মন্ত্রে উজ্জীবিত শিয়ারা ফি বছর লাঠিখেলা, তাজিয়া মিছিল আর মাতমে শরিক হন পহেলা মহররম থেকে। নানা মাধ্যমে নানাভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এই লড়াই আর আত্মত্যাগের মহিমা প্রচারিত হয়। নজরুল যেমন লর্ড ক্লাইভের দস্যুতাকে ‘সীমারের খঞ্জরে’ প্রতীকায়িত করেছিলেন, আয়াতুল্লাহ খোমেনি যেমন শাহের দুঃশাসনকে চিহ্নিত করেছিলেন এজিদের শাসনামল বলে, আগামীতেও তেমনি এই কারবালার কাহিনীকে কেন্দ্র করে নানা বিপ্লবের পুনরাবর্তন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।